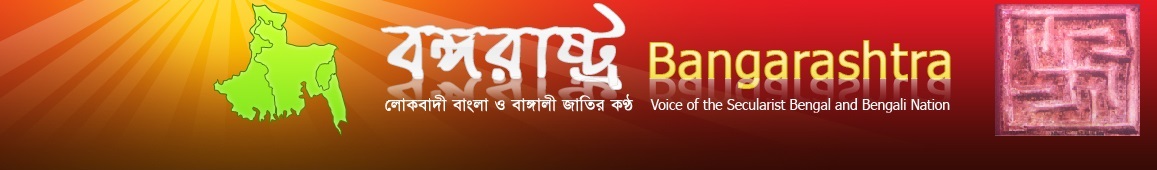জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ছন্দ – ইকবাল মাহমুদ
লিখেছেনঃ ইকবাল মাহমুদ, আপডেটঃ January 1, 2009, 12:00 AM, Hits: 11118
তিরিশের দশক ছিলো বাংলা আধুনিক কবিতার সোনালী সময়। এসময় বাংলা কবিতা যাঁদের হাতে গড়ে পিঠে ওঠে সেইসব আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ ছিলেন অন্যতম। আধুনিক এবং উত্তর আধুনিক সকল সমালোচকদের কাছে জীবনানন্দ ছিলেন এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি। তাঁদের ধারণা সময়ের আবর্তে ঘাত-প্রতিঘাতে, দু:খ, দৈন্য আর হতাশায় ডুবতে ডুবতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বেদতনায় ভারাক্রান্ত প্রকৃতির এক নি:সঙ্গ নিসর্গ প্রেমিক পুরুষ। সত্যি কি তাই? না তাঁর কাব্য যুগের সংশয়ী মানবাত্নার ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত অতীত ইতিহাসের কথা বলে? না তাঁর কাব্য সময়, সভ্যতা, রাজনীতি, ইতিহাস, প্রেম ইত্যাদির কথা বলে ইনিয়ে বিনিয়ে? এ বিতর্ক আগে ছিলো, এখনো আছে আধুনিক, উত্তর আধুনিক কবি তথা বোদ্ধা সমালোচকদের কাছে। আসলে তাঁর কাব্য পৌষের চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির প্রকৃতির মতো ছিলো কুহেলি কুহকে আচ্ছন্ন। তাঁর সাথে ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা, মানুষ, মানুষের ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয়, রাজনীতি ও সময়ের পিঠে চড়ে বসা সময় উঠে এসেছে প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে-রূপকল্পময়তার মধ্য দিয়ে। তাঁর কাব্যে মানুষী প্রতিচ্ছবি-পরিচয় ফুটে উঠেছে এক নিগূঢ় অভিযাত্রাকে লক্ষ্য করে।
রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক – জীবনানন্দ দাশের কবিতা হলো ‘চিত্ররূপময়’। শিল্পী যেমন কোন বিষয় বা বস্তুকে একঝলক দেখে নিয়ে রং আলো ছায়া যেমনটি দেখেছেন তেমনটি এঁকে বসিয়ে দিতে চান। সেখানে ছবির খণ্ডাংশের যেমন কোন অর্থ হয় না – সব মিলিয়ে একটা সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টি করাই যার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য – জীবনানন্দ দাশের কবিতাও ঠিক তাই। সাধারণত কবিতায় কী থাকে? কবিতায় থাকে বিষয়বস্তু, কাহিনীর ঘনঘটা, রূপ প্রকল্প, উপমা, শব্দ এবং ছন্দ। সকল কবির কবিতাতেই ছন্দ থাকে। ছন্দ মানেই হলো, উচ্চারণে ধ্বনি ও যতির আবর্তন। ধ্বনি ও যতির আবর্তন হলো কবিতার উচ্চারণে কোথায় থামতে হবে, কতটা সময় দিতে হবে, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন তার একটা প্রত্যাশিত নিয়ম। তবে তা ব্যাকরণ নয়। সাধারণ পাঠক কবিতা পাঠ করলে যে ভাব ও ধ্বনি-স্পন্দনের মাধুর্য উপভোগ করেন, সেই ছন্দবোধ ও উচ্চারণীয় আবেগীয় ভাবই হলো ধ্বনি ও যতির আবর্তন। ছন্দের যারা কারিগর, ছন্দ নিয়ে যারা নিয়ত খেলা খেলে থাকেন জীবনানন্দ তাদের থেকে একটু আলাদা। আলাদা এজন্যে যে, তাঁর কবিতার ছন্দ নির্দিষ্ট কোন নিয়ম বা নিয়মের বেড়াজালে বন্দী থেকে আমাদেরকে ভাবকল্পলোকের রাজ্যে নিয়ে যায় না। চটুল ও স্বাভাবিক ছন্দে অস্পষ্ট বিষয়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষে পুরো বিষয়কে বুঝিয়ে দেন ইমপ্রেশনিস্টদের মতো। ইমপ্রেশনিস্টদের মতো তিনি কোন বস্তুকে অবহেলা করেননি, বরং তার প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছেন। এবং সেই বিষয়বস্তুকে দেশজ শব্দের মেলবন্ধনে ছন্দের নিপুন ভঙ্গিমায় কবিতায় প্রকাশ করেছেন। জীবনানন্দের ছন্দ এবং শব্দ সম্বন্ধে অসাধারণ দখল থাকা সত্ত্বেও তাঁর পয়ারের বিস্তৃতির মধ্যে এমন এলানো ছড়ানো ভাব আছে যার জন্যে দৃঢ়বদ্ধতা দেখানো অসম্ভব। এমনকি যখন তিনি সনেট লিখেছেন তখনো তাকে বাইশ বা ছব্বিশ মাত্রার বিস্তৃতি দিয়েছেন। সনেটে সাধারণত ছন্দ থাকে। সাহিত্যে সনেট কবির ভাব প্রকাশের একটি সুপরিচিত এবং বিশেষ মর্যাদা প্রণালী। সনেটের প্রথম জন্ম ইতালীতে। সনেটের ইতিহাস পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে এর আয়তন, আকার ও মিলন পদ্ধতি শ্রেণী বিশেষের ভাব প্রকাশে বিশেষ উপযোগী বলেই সাহিত্যে এর প্রতিষ্ঠা। “যখন কোন মুহূর্তে প্রবল ভাবের আবেশে সমাচ্ছন্ন কবি হৃদয় সৌন্দর্যের দৈব আবির্ভাবে জাগ্রত হয়ে উঠে, সনেট ভাষা ও ছন্দে সেই দুর্লভ মুহূর্তের চিত্র।”(সমালোচনা সাহিত্য – শ্রী শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র পাল)
উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে সনেটের রচনার মূলে প্রবলভাবের প্রণোদনা চাই। কোন কোন সনেট আবার গভীর চিìতাশক্তি প্রসূত–শেক্সপীয়র যাকে (Deep
brained) সনেট বলেছেন। সুতরাং ভাব ও রসের একাগ্রতা সনেটের জীবন তৎপক্ষে ভাষা ও ছন্দের সংযম ও প্রণোদনা আবশ্যক।
“সনেটে চতুর্দ্দশপদ-ই সমীচীন এবং তাই সাহিত্য সংসারে বিরাজ করছে। চতুর্দ্দশপদ দু’ভাগে বিভক্ত। প্রথম আটপদ-Octavo-অষ্টক; অবশিষ্ট ছয়পদ-Sestet-ষষ্টক। সনেট মোট চৌদ্দটি পদে পরিমিতি। অষ্টকের আটটি পদে দুইটি মাত্র বিভিন্ন রসাত্নক মিল নিম্নলিখিতরূপে বিন্যস্ত হবে: প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম পদের মিল এক স্বরাত্নক। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পদের মিল আর এক স্বরাত্নক। যথা: ক–খ–খ–ক–ক–খ–ক। ষষ্টক মিলের একটু স্বাধীনতা আছে। তিনটি বিভিন্ন স্বরাত্নক মিলও ব্যবহৃত হতে পারে।’ (সমালোচনা সাহিত্য – শ্রী শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র পাল) এবং এই নিয়মেই আধুনিক কালের কবিরা সনেট লিখে থাকেন। সুতরাং সনেটের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও আলোচনার বিষয় যেহেতু ছন্দ সেহেতু ছন্দের সাথে সনেটের যেমন মিল রয়েছে তেমনি সনেটের সাথে ছন্দের। কেননা ছন্দের কথা বলতে গেলে সনেটের কথা আসবেই। মূল আলোচনায় যাবার আগে ছন্দ সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে জীবনানন্দের ছন্দ কুশলতা বিষয়টি পরিষ্কার করা দুরূহ হবে।
আধুনিক বাংলা কবিতা স্বয়ম্ভু নয়। এবং এ কারণেই বাংলা ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাসে আধুনিক কবিতার বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। গত অর্ধশতাব্দীকালের বেশি সময় ধরে কবি ও ছান্দসিকরা পাঠককে ছন্দ-প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেবার চেষ্টা করে চলেছেন। তিন প্রকৃতির ছন্দ রবীন্দ্রনাথের সময় থেকেই বাংলা পদ্যে উচ্চারণগত সুনির্দিষ্টতা লাভ করেছে। তা হলো : মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। এই তিন শ্রেণীর ছন্দেই মুক্তাক্ষর সর্বদা একমাত্র হ্যাঁ, না, সে ইত্যাদি। বদ্ধাকর স্বরবৃত্ত ছন্দে সর্বদা একমাত্রা, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সর্বদা দু’মাত্রা এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দের আদি মধ্যে একমাত্রা ও শেষে দু’মাত্রা। অর্থাৎ ‘বন্ধুর’ শব্দটি স্বরবৃত্তে দু’মাত্রা, মাত্রাবৃত্তে চারমাত্রা এবং অক্ষরবৃত্তে তিন মাত্রা। সুতরাং বদ্ধাক্ষরের মাত্রা গণনাভেদে বাংলা ছন্দত্রয় চিত্রিত। বাংলা ছন্দত্রয়ের মধ্যে প্রসারগুণে অক্ষরবৃত্ত অদ্বিতীয়। এর মধ্যযুগীয় নাম পয়ার। ৮€৬ পর্বদ্বয় বিভক্ত ১৪ মাত্রার দু’টি সমিল চরণ, প্রথম চরণের শেষে এক দাঁড়ি ও দ্বিতীয় চরণের শেষে দু’দাঁড়ি। ১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত অর্থাৎ পয়ারের এই ক্লান্তিকর আকৃতি পরিবর্তনের কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের। “মধুসূদনের হাতে বিবর্তিত অক্ষরবৃত্তের নাম অমিল প্রবহমান যতিস্বাধীন ১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। প্রচলিত নাম অমিত্রাক্ষর। মধুসূদনের প্রধান কৃতিত্ব বাংলা কবিতার পঠনরীতির পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা। হাজার বছরের বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে বাংলা অক্ষরবৃত্তের নতুন ও সম্ভাবনাময় দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের পরে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর কবিদের হাতে এই অক্ষরবৃত্ত পূর্ণতর রূপ লাভ করেছে।”
(আধুনিক বাংলা সাহিত্য – মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান)
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রবীন্দ্র নিরীক্ষার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ‘রাজা ও রানী’ নাটকে। এই নাটকের কাব্য সংলাপে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন–
‘ইলারে দেখিয়া যাবে?
কী হইবে দেখে তারে! কি হইবে দেখা
দিয়ে! স্বার্থপর! রয়েছ মৃত্যুর মুখে
অপমান বহ্নি–গৃহহীন, আশাহীন,
কেন আসিয়াছ ইলার হৃদয় মাঝে
জাগাতে প্রেমের স্মৃতি?’
(রাজা ও রানী – রবীন্দ্র রচনাবলী)
১৪ মাত্রার প্রবহমান স্বাধীন যতি অক্ষরবৃত্তের প্রথম দু’টি অমিল ও শেষ দু’টি সমিল। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সমিল অমিল উভয়রীতিই ব্যবহার করেছেন। মধুসূদন-রবীন্দ্রপথ অনুসরণ করেই রবীন্দ্রোত্ত আধুনিক কবিরা বাংলা আধুনিক কাব্যে যতিস্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করলেন।
ছন্দের দিক দিয়ে আধুনিক কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর প্রধান সাধনা ছিল বাক্ ছন্দের সঙ্গে কাব্য ছন্দের মিলন। বুদ্ধদেব দেখলেন বাক্রীতির সঙ্গে কাব্যরীতি মেলাতে হলে পয়ারই শ্রেষ্ঠ বাহন। বস্তুত বাঙালীর কথা বলবার স্বাভাবিক ছন্দই পয়ার ছন্দ। তার কারণ পয়ারের স্থিতিস্থাপকতা গুণ, অফুরন্ত সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীলতা। একমাত্র এই ছন্দেই লঘু ও ভারবান, দ্রুত ও মন্থর, গভীর ও চপল সবকটি সুরই বাজানো চলে। পয়ারের পরেই পড়ার ছন্দ। এই ছন্দই আমাদের মৌলিক ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি। যদিও পয়ারের বিþ—ক্সতি স্বরপ্রধানে নেই তবু কথ্যভাষার সঙ্গে সংযোগ অনেক বেশি। বুদ্ধদেব বসু এক্ষেত্রে খুব একটা সফল হননি। তিনি কথ্যরীতির সঙ্গে কাব্যরীতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে মাত্রা প্রধান ছন্দে আশ্রয় নিয়েছেন। মাত্রাপ্রধান ছন্দে কথ্যরীতির প্রকাশ কঠিন। কারণ এ ছন্দ অত্যন্ত আঁটোসাঁটো। পয়ারের সঙ্কোচ ও প্রসারণশীলতা এতে একেবারেই নেই। এর ফলে তাঁর ‘কঙ্কাবতী’ কাব্যে এক অদ্ভূত গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হয়েছে। ‘কঙ্কাবতী’র অধিকাংশ ছন্দের মূল সঙ্কেত ৬+৬+৫, কিন্তু কবি পর্বের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাঁর প্রসার বিস্তার করেছেন। যথা –
তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো
পৃথিবী শেষ সীমা যেখানে চারিদিকে খালি আকাশ ফাঁকা।
বুদ্ধদেব বসুর এ ছন্দরীতি অপেক্ষাকৃত লঘুরসের – কিছুক্ষণ পর এ ছন্দ একঘেয়ে ঠেকে। অক্ষরবৃত্ত তথা যতি স্বাধীন অক্ষরবৃত্ত ব্যবহার করে জীবনানন্দ দাশ কবিতায় এক নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছেন। তিনি অধিকমাত্রা ব্যবহার করে সমিল অমিল উভয়ভঙ্গিতে স্বাধীন যতি অক্ষরবৃত্ত রচনা করেছেন। এমনই একটি কবিতা–
আহ্লাদের অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া–রোদ–খুদ–কুঁড়ো– কার্তিকের ভিড়,
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান
পাড়াগাঁর গায়ে আজ লেগে আছে রূপশালী ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।
(অবসরের গান – ধূসর পাণ্ডুলিপি)
প্রথম দু’টি চরণে ১৮ মাত্রা, তৃতীয় চরণে ২৬ মাত্রা এবং চতুর্থ চরণে ৩০ মাত্রা। উদ্ধৃত কবিতাটি সমিল।
মূলত জীবনানন্দ দাশ ছিলেন ছিলেন তান প্রধান কবি। বুদ্ধদেব বসুর মতো তাঁরও স্বাতন্ত্র্য অসম পয়ার ও বলাকার ছন্দ রচনায়। এমনি একটি কবিতা ‘নীলিমা’। যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে অসম পয়ার। শুধু তাই নয় তাঁর এ কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব ও ছন্দ প্রকরণ অত্যন্ত সাবলীলভাবে ধরা পড়েছে। যেমন–
অগনন যাত্রিকের প্রাণ।
খুঁজে মরে অনিবার, পায় নাকো পথের সন্ধান;
চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল,–
হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ্য বিধি-বিধানের এই কারাতল
তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছো মায়াবী।
জনতার কোলাহলে একা ব’সে ভাবি
কোন দূর জাদুপুর – রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি’
বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী;
স্ফটিক আলোকে তব বিথারিয়া নীলাম্বরখানা
মৌন স্বপ্ন ও ময়ূরের ডানা !
(নীলিমা – ঝরাপালক)
অথবা,
একে একে ডুবে যায় দেশ, জাতি, সংসার সমাজ
কার লাগি, হে সমাধি, তুমি একা বসে আছ আজ
কি এক বিক্ষুব্ধ প্রেতকায়ার মতন !
অতীতের শোভাযাত্রা কোথায় কখন
চকিতে মিলায়ে গেছে, –পাও নাই টের !
কেন দিবা অবসানে গৌরবের লক্ষ মুসাফের
দেউটি নিভায়ে গেছে, –চলে গেছে দেউল ত্যজিয়া,
চলে গেছে প্রিয়তম, –চলে গেছে প্রিয়া।
(পিরামিড – ঝরা পালক)
অথবা,
পৃথিবীর প্রেতচোখ বুঝি
সহসা উঠিল ভাসি, তারকা-দর্পণে মোর অপহৃত আননের প্রতিবিম্ব খুঁজি’ !
ভ্রূণ-ভ্রষ্ট সন্তানের তরে
মাটি-মা ছুটিয়া এল বুক-ফাটা মিনতির ভরে,–
সঙ্গে নিয়ে বোবা শিশু,–বৃদ্ধ মৃত পিতা
সূতিকা-আলয় আর শশ্মানের চিতা।
(সেদিন এ ধরণীর – ঝরা পালক)
জীবনানন্দের ‘নীলিমা’, ‘পিরামিড’ ও ‘সেদিন এ ধরণীতে’ এ তিনটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। ‘ঝরাপালক’-এর যুগ থেকে তিনি ছন্দে দক্ষতা দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয় ‘ঝরাপালক’-এর যুগে তিনি বিভিন্ন ছন্দে লিখেছেন – কখনো ধ্বনি প্রধান ছন্দে, কখনো স্বরপ্রধানে আবার কখনো অসম পয়ারে। কিন্তু শেষের দিকে এসে তিনি গদ্য ও তানপ্রধান ছন্দে লিখেছেন। মূলত তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলো তানপ্রধান ছন্দেই লেখা। তাঁর ‘মরীচিকা’ কবিতাটি ধ্বনি প্রধান ছন্দে লেখা। যেমন–
কে যেন রেখেছে সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা পাতি!
যত খুন যত খারাবীর ঘোরে পরান আছিল মাতি,
নিমেষে গিয়েছে ভেঙে
স্বপন-আবেশে রেঙে
আঁখি দু’টি তার জৌলস্ – রাঙা হ’য়ে গেছে রাতারাতি
কোন্ যেন এক জিন-সর্দার সেজেছে তাহার সাথী।
(মরীচিকার পিছে – ঝরাপালক)
অথবা,
আমি প্রজাপতি মিঠা মাঠে মাঠে সোঁদাল সর্ষে ক্ষেতে
– রোদের শর্করে খুঁজি না ক’ ঘর
বাঁধি না ক’ বাসা, – কাঁপি থর থর
অতসী ছুঁড়ির ঠোঁটের উপর
শুঁড়ির গেলাসে মেতে।
... ... ...
আমি গো লালিমা, গোধূলী সীমা – বাতাসের ‘লালাফুল’
... ... ... ...
আমি খুশরোজী – আমি গো খেয়ালী,
চঞ্চল – বুলবুল।
(যে কামনা নিয়ে – ঝরাপালক)
এ দু’টি কবিতায় নজরুলের কণ্ঠ চেনা যায়। নজরুলের কবিতায় সবসময় ধ্বনি প্রধান ছন্দে চটুল ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। নজরুল ইসলাম শ্বাস যতি অনুসরণ করে কবিতা লিখলেও মূলত তাঁর কৃতিত্ব ছিলো মাত্রাবৃত্তে। নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবনানন্দ মাত্রাবৃত্ত, ধ্বনি প্রধান ছন্দ ও চটুল ভাষায় অনেক কবিতা লেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ‘সাগর বলাকা’ কিংবা ‘বনের চাতক-মনের চাতক’ কবিতায় ধ্বনি প্রধান ছন্দের ব্যবহার বেশি পরিলক্ষিত হয়। যেমন–
ননীর কলস আছে রে তোর কাঁচা বুকের কাছে,
আতার ক্ষীরের মত সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে
(বনের চাতক-মনের চাতক–ঝরাপালক)
অথবা,
বাসা তোমার সাত সাগরের ঘূর্ণি হাওয়ার বুকে !
ফুটছে ভাষা কেউটে ঢেউয়ের ফেনার ফণা ঠুকে।
প্রয়াণ তোমার প্রবাল দ্বীপে, পলার মালা গলে
বরুণ রানী ফিরছে যেথা, – মুক্তাপ্রদীপ জ্বলে।
(সাগর বলাকা – ঝরাপালক)
এ দু’টি কবিতা ধ্বনি প্রধান ছন্দে লেখা। উল্লেখ্য যে ‘ঝরাপলক’ কাব্যের যুগ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যুগ দ্বারা প্রভাবিত। ‘ঝরাপলক’ সম্ভবত ১৩৩৪ সালে বেরিয়েছিলো এবং তার রচনাকাল আরো কিছু আগে হবে হয়তো। মোহিতলাল মজুমদার এর স্বপনপসারীর মত, ‘ঝরাপলক’কেও সত্যেনন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব স্পষ্ট। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিশেষ করে আঙ্গিক ও ছন্দ বৈচিত্র্যের জন্য তরুণ কবিদের কাছে প্রিয় ছিলেন। তাঁর ধ্বনাত্নক শব্দের ব্যবহার, বিভিন্ন ছন্দের অনুসরণ, গ্রাম্য ও লৌকিক শব্দ সম্বন্ধে ঔদার্য বলা বাহুল্য নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। বাংলা ভাষায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সংস্কৃত ছন্দ পরীক্ষা যেমন সুধীন্দ্রনাথ কে আকৃষ্ট করেছিল ঠিক তেমনি আকৃষ্ট করেছিল জীবনানন্দ দাশকেও। যেমন–
ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল–
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, পাকা আপেলের মত লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁিখ যার গোধূলির মত গোলাপি রঙিন,
তারে আমি দেখিয়াছি প্রতি রাত্রে– স্বপ্নে– কতদিন।
সত্যেন্দ্রনাথ ঝঙ্কার থেকে এ অনেক দূরে; অতি পুরনো কল্পনা যেন একটি নতুন ভাবনা ও তাড়না দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে ছন্দের নবত্ব ও ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে কাব্যে অপূর্ব রূপ পেয়েছে। এ যেন শিল্পীর তুলিতে একটানে আঁকা পুরো একটি ছবি যা রচনার কলাকৌশলের দ্বারা শিল্পীর নিজস্বতা-সৃষ্টি প্রেরণার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি ধ্বনি প্রধান ছন্দে লেখা কবিতায় তিনি ব্যবহার করেছেন নাম ও বিদেশী শব্দ এবং ইংরেজী শব্দগুলোকে বাঙলার প্রকৃত ছন্দের সাথে এমনভাবে মেশানো হয়েছে যে আশ্চর্য বলতে হয়। যেমন–
সাগরের অই পারে– আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখী ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের ’পর
নেমেছিল তারা তারপর,–
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।
বাদামি– সোনালী– শাদা– ফুটফুটে ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল,–
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ’রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হয়ে!
(পাখীরা – ধূসর পান্ডুলিপি)
এ কবিতার ধ্বনি উচ্চ নয় তীব্র নয়, কিন্তু গভীর ও প্রতিধ্বনিময়। এখানে নাম-শব্দ ব্যবহার করেছেন জমকালো ধ্বনি সৃষ্টির জন্যে নয়, প্রির্যা ফেলাইটদের মত ছবি ফোটাতে। নাম ও বিদেশী শব্দের পাশাপাশি ইংরেজী শব্দগুলোকে বাঙলার প্রকৃত ছন্দের সঙ্গে এমনভাবে মেশানো হয়েছে যে আশ্চর্য বলতে হয়। এখানে যুক্তাক্ষর কম – যুক্তাক্ষরের অভাবে পয়ার শিথিল ও মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েনি। এখানে যুক্তাক্ষরের স্বল্পতা পয়ারে এনেছে এক নতুন সুর।
ছন্দ নিয়ে একসময় জীবনানন্দ দাশ ভালোই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর কাব্যে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীতে তাঁর ছন্দ হয়ে উঠেছে হয় তান প্রধান নয় তো পয়ার। মূলত তাঁর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো বাক্রীতি ও কাব্যরীতির মিলন। কথ্যভাষার প্রবহমানতা, গাম্ভীর্য এবং স্বাভাবিক রীতি তিনি কাব্যে দান করেছেন। তাছাড়া যুগের ক্লান্তি, হতাশা, তিক্ততা, স্মৃতি, প্রেরণা, জীবন-মৃত্যু প্রভৃতি ভাবনা, সুরগুলিকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন এই তান প্রধান ছন্দের মাধ্যমে। ‘ধূসর পান্ডুলিপি’র কথা ধরা যাক। এই কাব্যগ্রন্থের সবগুলো কবিতা পয়ার ছন্দে লেখা – বেশিরভাগ কবিতাই পয়ার অসম মাত্রার। যাকে বলাকার ছন্দ বললে খুব বেশি ভুল হবে না। অর্থাৎ চেহারাটা বলাকার ছন্দের কিন্তু ধ্বনি একেবারেই ভিন্ন। যেমন–
হলদে পাতার মত আমাদের ওড়াউড়ি
কবরের থেকে শুধু আকাঙ্খার ভূত ল’য়ে খেলা। –
আমরা ও ছায়া হ’য়ে – ভূত হ’য়ে করি ঘোরাঘুরি!
... ... ... ...
শরীর রয়েছে তবু ম’রে গেছে আমাদের মন ?
হেমন্ত আসেনি মাঠে, – হলদে পাতায় ভরে হৃদয়ের বন ?
(জীবন – ধূসর পাণ্ডুলিপি)
অথবা,
শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার-চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়;
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট ক’রে দেবে তার সাধের সময়।
... ... ... ... ...
অনেক রাতের আগে এসে তারা চ’লে গেছে – তাদের দিনের আলো হয়েছে আঁধার,
সেই সব গেঁয়ে কবি-পাড়াগাঁর ভাঁড়
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর?
(অবসরের গান – ধূসর পাণ্ডুলিপি)
এ দু’টি কবিতায় বলাকার তীব্রতা ও বেগ একেবারেই নেই। এখানে ছন্দ মন্থর, যেন ভাঙা ভাঙা, অসমান ও পালিশ না করা। এখানে ছন্দ থেমে-থেমে, ঘুরে-ঘুরে চলে, ঘুমে ভরা সুর, স্বপ্নে ভরা, শিশির কোমল, যেন ঘুমের মধ্যে গান এসে কানে লাগে, তারপর সমস্ত রাত হানা দেয়। এখানে ২২, ২৬ ও ২৮ মাত্রার দীর্ঘতম চরণ ব্যবহার করা হয়েছে। চরণটি মোট ৩০ মাত্রার। পয়ার ছন্দের কবিতায় জীবনানন্দ প্রথাবদ্ধ ২, ৪, ৬, ৮ চরণের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। যেমন ‘হায় চিল’ কবিতা। এ কবিতাটি ৯ চরণে সমাপ্ত হয়েছে। কিংবা ‘অনেক আকাশ’।
গানের সুরের মতো বিকালের দিকের বাতাসে
পৃথিবীর পথ ছেড়ে সন্ধ্যার মেঘের রং খুঁজে
হৃদয় ভাসিয়া যায় – সেখানে সে কারে ভালবাসে!–
পাখির মতন কেঁপে – ডানা মেলে – হিম চোখ বুঁজে
অধীর পাতার মতো পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে উড়ে ঘর ছেড়ে কতদিকে গিয়েছে সে ভেসে,–
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুঁজে
ঘুমাতে চেয়েছে,– তবু – ব্যাথা পেয়ে গেছে ফেঁসে।
তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁটে উঠেছিল হেসে।
(অনেক আকাশ – ধূসর পাণ্ডুলিপি)
‘অনেক আকাশ’ কবিতার শব্দ সঙ্কেত এই রূপ– ক খ ক খ, খ গ খ গ গ। প্রথম আট লাইন ৮-১০ মাত্রাভাগের মহাপয়ার, নবম লাইনটি দীর্ঘতর। জীবনান্দ প্রথম সাত লাইন ৮€১০ মাত্রাভাগে, অষ্টম লাইনটি দু’মাত্রা কম রেখে ৮€৮-মাত্রাভাগে, এবং নবম লাইন দীর্ঘতর ৮€৮€৬ মাত্রাভাগে রচনা করেছেন। সনেটের ক্ষেত্রে জীবনানন্দের কবিতায় চরণের স্তবক ও প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে বাকরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ সহজ হয়েছে।
অথবা,
কি এক ইশারা যেন মনে রেখে একা-একা শহরের পথ থেকে পথে ক
অনেক হেঁটেছি আমি; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম বাস সব ঠিক চলে; খ
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে : ক
সারারাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে। খ
কেউ ভুল করে নাকো – ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব গ
চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে। খ
একা-একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব; ঘ
তখন অনেক রাত – তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা গ
নির্জনে ঘিরেছে এসে;– মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব ঘ
আর কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা আর মনুমেন্ট ভরা কলকাতা? ঙ
চোখ নিচে নেমে যায়–চুরুট নীরবে জ্বলে বাতাসে অনেক ধুলো খড়; ঘ
চোখ বুঁজে একপাশে সরে যাই – গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ
পাতা ঙ
উড়ে গেছে; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর ঙ
কেন যেন; আজো আমি জানি নাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর! ঙ
(পথ হাঁটা – বনলতা সেন)
এ দু’ট কবিতা ৮+৮+১০=২৬ মাত্রার। সনেট রচনায় জীবনানন্দ দান্তে প্রবর্তিত তের্জারিমা ত্রি-পংক্তির স্তবকের ব্যবহার করেছেন। প্রমথ চৌধুরী বাংলা কবিতায় এ ত্রিক মিলবন্ধনের প্রবর্তন করেছিলেন। জীবনানন্দ তাকে সনেটের আঙ্গিকে প্রয়োগ করলেন। ‘শকুন’ কবিতাটি পড়লে দেখা যায় প্রত্যেক ত্রিক এর মধ্য পঙক্তিটি মিলহীন। প্রথম পংক্তি ও তৃতীয় পংক্তিতে মিল। আবার শেষে এসে শ্লোক বন্ধনের মিল। যেমন–
মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে–সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে ক
শকুনেরা চরিতেছে; মানুষ দেখেছে হাট, ঘাঁটি বস্তি; নিস্তব্ধ প্রান্তর খ
শকুনেরা; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে ক
আরেক আকাশ যেন – সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর খ
কঠিন মেঘের থেকে; যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্হস্তিগণ গ
পড়ে গেছে–পড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার খেত মাঠ প্রান্তরের পর খ
এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মূহূর্ত শুধু; আবার করিছে আরোহণ গ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে–পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে; ঘ
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে, বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন গ
বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দ্যাখে তাই; একবার স্নিগ্ধ মালাবারে ঘ
উড়ে যায় – কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন ঙ
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর উপরে; ঘ
যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ-জীবনের বিচ্ছেদের বিষণí লেগুন ঙ
কেঁদে ওঠে...চেয়ে দ্যাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হুন। ঙ
(শকুন – ধূসর পাণ্ডুলিপি)
এখানে সব লাইনই ৮+৮+১০ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপকীবন্ধে আবদ্ধ। অবশ্য মাঝে মাঝে যতি স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায়। জীবনানন্দ সনেটে পেত্রার্কীয় ধারা ব্যবহার করলেও ষষ্টকে তিনি বিশেষ স্বাধীনতা নিয়েছেন। ষষ্টকে পেত্রার্কের অন্ত্যমিল দু’প্রকার : এক, কখ কখ কখ, দুই, কখগ কখগ। জীবনানন্দেও শেষ ছয় লাইনের অন্ত্যমিল পেত্রার্কীয় না হলেও তিনি সংখ্যা ঠিক রেখে চাল ঘুরিয়ে দেন – পেত্রার্ক নিজে ও ষষ্টকে এমন পরিবর্তন এনেছেন। পেত্রার্কীয় ধারায় সনেট রচিত মাত্রা চারটি (অথবা পাঁচটি) অন্ত্যমিলের মাধ্যমে। পেত্রার্ক-এর সনেট অষ্টম ও ষষ্টক এর নিয়মে বন্দী। ষোড়শ শতাব্দীতে শেক্সপীয়র (১৫৪৬–১৬১৬) প্রেত্রার্কীয় সনেটের বাঁধাবাঁধি নিয়ম অষ্টক এবং ষষ্টক (আট-ছয়) মুল কাঠামো ঠিক রেখে অন্ত্যমিলের নতুন বিন্যাসে ৪+৪+৪+২ স্তবকে আরো সহজতর করে তোলেন। যদিও অষ্টম চরণে প্রায়ই ভাবের বিরাম দেখা যায়। শেক্সপীয়র এর সনেটে প্রথম দ্বাদশ চরনে তিনটি চতুর্দ্দশপদী গঠিত। এখানে মিল বা মিত্রাক্ষর-সংস্থান এক ছত্রান্তর পর্যায়ে বিন্যস্ত, এবং প্রত্যেক চতুর্দ্দশপদীতে দুটি বিভিন্ন স্বরাত্নক মিল থাকে –শেষ দু’টি চরণ মিত্রাক্ষর পয়ার এবং শেষ দুই চরণেই শেক্সপীয়র এর বিশেষত্ব। হয় এ দু’টি পদে পূর্ব্বগত তিনটি চতুদ্দর্শপদীয় সমুদয় ভাব ও রস সমষ্টি আকারে চরণমাত্রা লাভ করবে না হয় বিপরীতভাবের সমাবেশ সংঘর্ষণে পদ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। চারটি অন্ত্যমিলে সনেট রচনা খুবই দুরূহ কাজ – আর যদি তাকে একটি উৎকৃষ্ট কবিতা হিসেবে দাঁড় করাতে হয় তবে সেটা আরো কটিন কাজ। কিন্তু সেই দুরূহ কাজটি জীবনানন্দ দাশ করেছেন অত্যন্ত সুচারুরূপে। চৌদ্দ পঙক্তির অবকাঠামো ঠিক রেখে তিনি বেশ কিছু সনেট রচনা করেছেন। যেমন, তাঁর ‘একদিন জলসিঁড়ি’ কবিতা।
একদিন জলসিঁড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
বিশীর্ণ বটের নিয়ে শুয়ে রবো; পশমের মতো লাল ফল
ঝরিবে বিজন ঘাসে,– বাঁকা চাঁদ জেগে র’বে – নদীটির জল
বাঙালী মেয়ের মতো বিশালক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাটে
আঘাত করিয়া যাবে ভয়ে-ভয়ে – তারপর যেই ভাঙা ঘাটে
রূপসীরা আজ আর আসে নাকো, পাট শুধু পচে অবিরল,
সেইখানে কলমির দামে বেঁধে প্রেতিনীর মতন কেবল
কাঁদিবে সে সারা রাত,– দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে
সাজায়ে রেখেছে চিতা; বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ
চেয়ে রবে; ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে
শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প– ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে;
চারিদিকে বাংলার ধানী শাড়ি– শাদা শাঁখা– বাংলার ঘাস
আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীল মঠ– আপনা মনে
ভাঙিতেছে ধীরে-ধীরে;– চারিদিকে এইসব আশ্চর্য উচ্ছ্বাস–
(একদিন জলসিঁড়ি – রূপসী বাংলা)
তিনি পেত্রার্কীয় ও শেক্সপীয়রীয় উভয় রীতিকেই মিশ্রিত করেছেন। জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সব কৌশলগুলিই প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ের জন্য। ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় সনেটের এ বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বলভাবে আমাদেও সামনে ফুটে উঠে। আবার মধ্য মিলের ছন্দও জীবনানন্দের কাব্যে প্রকট। ‘বনলতা সেন’ কিংবা ‘মনে পড়ে কবেকার পাঁড়াগায় অরুণিমা স্যানালের মুখ’। অপরদিকে ‘হাওয়ার রাত’, ‘নগ্ন নির্জন হাত’, ‘ঘাস’, ‘শিকার’, ‘বেড়াল’ ইত্যাদি কবিতায় গদ্যছন্দের ব্যবহার অধিকমাত্রায়। তাঁর গদ্য কবিতায় নিরূপিত মাত্রার হিসাব থেকে ছন্দ পুরোপুরি মুক্তি পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেন’, ‘মহাপৃথিবী’, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ – কাব্যগ্রন্থ তিনটি উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্যের উদাহরণ। এখানে ছোট ছোট বাক্যের আবর্তন, এক ধরনের শব্দ বিন্যাসের আবর্তন এবং প্রচ্ছন্ন ধ্বনিগত আবর্তন অনুভব করা যায়। কবিতায় ভাব ও ধ্বনি এনে পাঠকের মনে এক ধরনের প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলেন। যেমন,
কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ’রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস – তেমনি সুঘ্রাণ –
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারো ইচ্ছে করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি – চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদু অন্ধকার থেকে নেমে।
(ঘাস – ধূসর পাণ্ডুলিপি)
অথবা,
যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে ম’রে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম’রে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূরে আকাশের সীমানায় কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা
হাতে করে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন –
(হাওয়ার রাত–ধূসর পাণ্ডুলিপি)
অথবা,
সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় :
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামি পাতার ভিড়ে;
কোথাও কয়েক টুকরা মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর সাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হ’য়ে আছে দেখি
কিন্তু তবুও তারপর কৃষäচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে পিছনে চলেছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রং-এর সূর্যের নরম শরীরে
সাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।
(বিড়াল – ধূসর পাণ্ডুলিপি)
ছোটো ছোটো বিষয়কে তিনি ছন্দের প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে, গদ্যে নিখুঁতভাবে ভাষা ও উপমার চাতুর্য্যে ভরে তুলেছেন। তাঁর শেষের দিকের কবিতাগুলো পড়লে এমনই মনে হয়। গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এরকম :
‘১। গদ্য কাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়; পদ্য কাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটা সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তা দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চারণ স্বাভাবিক হতে পারে –
২। গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রস রচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্য ছন্দ বোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজ না থাকে অলংকার শাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণে গদ্যছন্দ সহজ না।’[১]
গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে শেষ পর্যন্ত একটা সংস্কার দানা বেঁধেছিল : পদ্যের সলজ্জ সহজভাব ত্যাজ্য কিন্তু অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ছন্দ প্রতিপাল্য। ফলে রবীন্দ্র কবিতার গদ্যরূপ নিরূপিত। কবিতায় যখন ছন্দ, অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, সমিল–অমিল স্বাধীন যতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তখন কথ্যরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণে আর এক ছন্দের সৃষ্টি হল যার নাম গদ্যরীতির ছন্দ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এ ছন্দের প্রবর্তক। উদাহরণ স্বরূপ রীবন্দ্রনাথের ‘পুনশ্চ’ কবিতাটির কথা বলা যায়।
‘পুনশ্চ’ কবিতায় যে গদ্যরীতি আমরা পাই তা আধুনিক কবিদের ভালভাবেই নাড়া দিয়েছিল। আর তাতে মুগ্ধ হয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘নতুন পাতা’ কবিতা গদ্যরীতিতে লিখেছিলেন। যেমন –
তোমার উত্তাপ সঞ্চারিত হোক আমার রক্তে
তোমার অন্ধকারের নির্মম নিষ্পেষণে
আমি যেন উষ্ণ সুরার মতো ঝ’রে ঝ’রে পড়ি
তোমার প্রাণের নিভৃত পাত্রে
বিন্দু বিন্দু ক’রে
নি:শেষে।
(যে কোনো মেয়ের প্রতি – নতুন পাতা)
অথবা,
আর আমার মধ্যে কী যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে
পাথর যেমন ভেঙ্গে যায় পৃথিবীর অন্তর্লীন ভীষণ আগুনের চাপে।
আর আমার মধ্যে কী যেন গড়ে উঠছে, জ‘মে উঠছে,
... ... ... ... ...
এ কী আশ্চর্য মৃত্যু!
এ কী আশ্চর্য নতুন জন্ম!
(নতুন দিন – নতুন পাতা)
অথবা,
আর আমাকে টেনে নিয়ে তোমার কাছে,
... ... ... ...
টেনে নিয়ে সেই অতল অনির্বচনীয় অন্ধকারে
যেখানে ঝরছে তোমার সঙ্গোপন সূর্য
পল্লবের পর পল্লবে–
(সত্তায় – নতুন পাতা)
রবীন্দ্রনাথের মনের কোণে যে সংশয় বা সংষ্কার দানা বেঁধেছিল জীবনানন্দ তা মুছে দিতে পেরেছিলেন তাঁর ‘হাওয়ার রাত’, ‘ঘাস’, ‘বেড়াল’ কিংবা ‘নগ্ন নির্জন হাত’ ‘তোমাকে’-এর মতো আরো অনেক কবিতা দিয়ে। যেমন,
যদিও পথ আছে তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্নবোধের দীপের মতো
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব-সাগরে।
তবুও তোমায় জেনেছি নারী, ইতিহাসের
শেষে এসে; মানব প্রতিভার
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারী, শুধু তোমাকে ভালবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কীরকম মধুর হতে পারে।
(তোমাকে – বেলা অবেলা কালবেলা)
শেষে এ কথাই বলতে পারি যে স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, ধ্বনিবৃত্ত বা গদ্যছন্দ যেভাবে লিখে থাকেন না কেন, মূলত তাঁর ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিলো প্রচ্ছন্নতা – কলাকৌশলের নিপুণ ভঙ্গিমা – শব্দ ও ছন্দ নিয়ে জাদুকরী খেলা খেলার ক্ষমতা। ছন্দের প্রচলিত নিয়ম ভেঙে তিনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন এবং বেরিয়ে আসার প্রবণতা তাঁর রচনার মধ্যে ছিল। প্রথাগত মাত্রার হিসাব, পঙক্তি, যতির সুষম ভাগ রক্ষার বাধ্যবাধকতা তিনি সচেতনভাবেই ভাঙতে চেয়েছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভেঙেছেনও। যার ফলে ছন্দ তাঁর কোথাও টলেনি, মিল অনুপ্রাস, পুনরুক্তিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে; কিন্তু সেগুলি কোথাও চমক দেয় না। সব মিলিয়ে কবির বক্তব্যটিকে আরো স্ফুটন করে তোলে। আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কবিতা সন্ধান দেয় গভীরতর মননের স্তরে যাত্রী হবার।
সহায়ক গ্রন্থ
০১। ছন্দ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী
০২। ছন্দ ও কবিতা – অমিয় চক্রবর্তী
০৩। আধুনিক বাংলা কবিতা – আবু সয়ীদ আইয়ূব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)
০৪। জীবনানন্দ দাশের কবিতা সমগ্র – জীবনানন্দ দাশ
০৫। কাব্য সংগ্রহ – বুদ্ধদেব বসু (প্রথম সংস্করণ)
০৬। মধুসূদন – সৈয়দ আলী আহসান
০৭। আধুনিক বাংলা সাহিত্য – মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।
অনলাইন : ১ জানুয়ারি,২০০৯